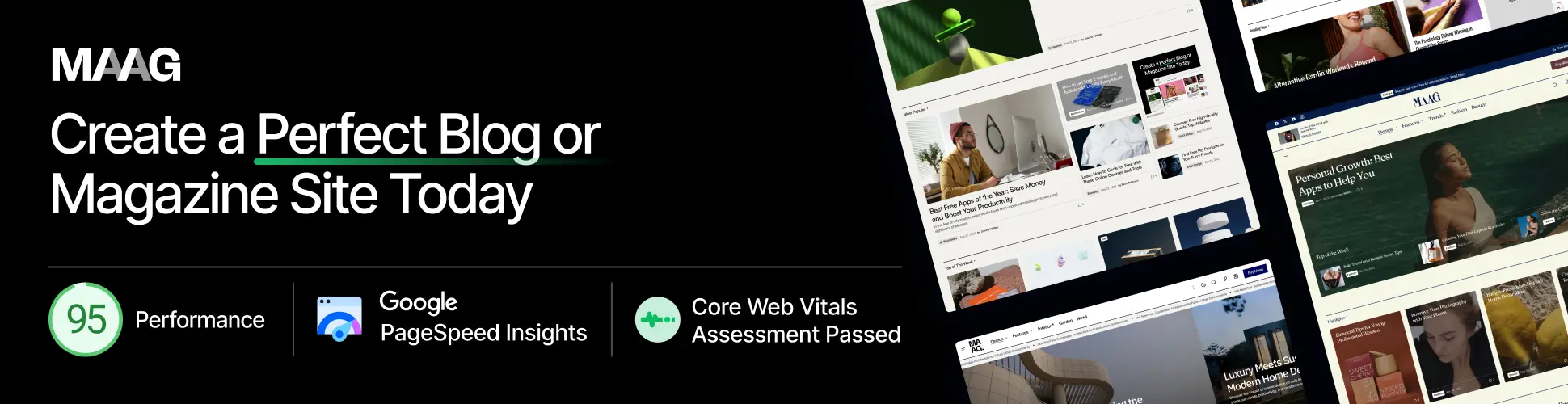দেশের একজন মানুষ এখন ৭৯.৬ ডলার ঋণের বোঝা বহন করছে। যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ এবং স্বল্পোন্নত দেশের গড় ঋণের প্রায় ৪ গুণ বেশি। বাংলাদেশের ঋণ-অনুদান অনুপাত ছাড়িয়েছে ২.৭। এটি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় প্রায় চারগুণ। এছাড়া বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক (এমডিবি) থেকে গৃহীত ঋণের অনুপাত ০.৯৪, যা বৈশ্বিক গড় ০.১৯ এর প্রায় পাঁচগুণ বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে ঋণের বোঝায় বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে।যদিও বাংলাদেশ বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের মাত্র ০.৫ শতাংশের জন্য দায়ী।
পাশাপাশি বাংলাদেশের জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন খাতের বিনিয়োগ অনুপাত মাত্র ০.৪২, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর গড় অনুপাতের অর্ধেকেরও কম। এর ফলে, জলবায়ু সহনশীলতা অর্জনের প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে অর্থায়নের অভাবে পড়ছে। আজ শনিবার রাজধানীতে চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ কর্তৃক প্রকাশিত ‘ক্লাইমেট ডেট রিস্ক ইনডেক্স (সিডিআরআই-২০২৫)’ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।
গবেষণার তথ্য অনুসারে, প্যারিস চুক্তির ‘ক্ষতিপূরণ’ হিসেবে প্রতিশ্রুত আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাটি কীভাবে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য একটি “জলবায়ু ঋণ ফাঁদে” পরিণত হয়েছে। জলবায়ু অর্থায়নের ৭০ শতাংশেরও বেশি আসে ঋণ হিসেবে, যা সংকটাপন্ন দেশগুলোকে দ্বিগুণ ক্ষতির মুখে ফেলছে: প্রথমত, দেশগুলো উপোর্যুপরি জলবায়ু ঘটিত বিপর্যয়ের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একইসাথে ঋণের ক্রমবর্ধমান কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ২০০০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের ১৩ কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৩৬০ কোটি মার্কিন ডলার। এতকিছুর পরেও জলবায়ু অভিযোজন খাতে সহায়তা নগণ্য। অন্যদিকে, দেশের পরিবারগুলো স্ব-অর্থায়নে জলবায়ু ঘটিত বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রতি বছর মাথাপিছু গড়ে ১০ হাজার ৭০০ টাকা (প্রায় ৮৮ মার্কিন ডলার) ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে, যা জাতীয় পর্যায়ে বার্ষিক ১৭০ কোটি মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. এ. কে. ইনামুল হক বলেন, “জলবায়ু বিজ্ঞান, তবু বাংলাদেশ গভীর ঝুঁকিতে। অনুদান সীমিত, ঋণের ঝুঁকি বেশি, বেসরকারি খাতে অতিনির্ভরতা আর্থিক চাপ বাড়ায়। ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের ওপর মানবপাচারের মতো হুমকিও থাকে। টেকসই শক্তি গড়তে স্থানীয় জ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা–পরিবর্তন দরকার—খণ্ড খণ্ড সমাধান যথেষ্ট নয়।”
বাংলাদেশের চিত্র:
ঋণ-অনুদান অনুপাত ২.৭, যেখানে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর গড় মান মাত্র ০.৭। বহুপাক্ষিক তহবিল থেকে পাওয়া জলবায়ু অর্থায়নের ঋণ-অনুদান অনুপাত ০.৯৪, যা স্বল্পোন্নত গড়ের (০.১৯) প্রায় পাঁচগুণ। অভিযোজন-প্রশমন অনুপাত মাত্র ০.৪২, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর গড় মানের (০.৮৮) অর্ধেকেরও কম। ‘পলিউটারস পে প্রিন্সিপাল’ নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন: প্রতি টন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের জন্য বাংলাদেশকে ২৯.৫২ মার্কিন ডলার ঋণ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। জলবায়ু অর্থায়নের অর্ধেকেরও বেশি জ্বালানি খাতে ব্যবহৃত হয়, যা মূলত ঋণ-নির্ভর (জ্বালানী খাতে ঋণ-অনুদান অনুপাত ১১.৯৯:১)। পরিবহন ও গুদামজাতকরণ খাতে অর্থায়ন প্রায় পুরোটাই ঋণ (ঋণ-অনুদান অনুপাত ১১২৩:১)। অভিযোজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পানি সরবরাহ খাতে ঋণের অনুপাত ৭.৭৮:১। অন্যদিকে, ঝুঁকি ও প্রয়োজনের তুলনায় কৃষি, দুর্যোগ প্রস্তুতি, স্বাস্থ্য এবং শিল্প খাত মারাত্মকভাবে স্বল্প অর্থায়ন পেয়েছে। বাংলাদেশের জন্য রিপোর্টকৃত “জলবায়ু” অর্থায়নের ১৮.৮৪% জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে ভুলভাবে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোতে ঋণ-অনুদান অনুপাত ২৮.৮, যা বাংলাদেশের সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং প্রকৃত জলবায়ু সমাধানকে বাধাগ্রস্ত করছে।
এ বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়েরে সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন “জীববৈচিত্র্য রক্ষা করলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমে, কিন্তু কপ এর মতো বৈশ্বিক ফোরামে বাস্তব ফল কম—ফলে মানুষ ঝুঁকিতে থাকে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায়ে উল্লেখিত অসম কার্বন নিঃসরণ প্রশ্নে বাংলাদেশকে সাড়া দিতে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও এনডিসি বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।”
বৈশ্বিক চিত্র:
সিডিআরআই-২০২৫ সূচকে ৫৫টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, ১৩টি দেশ অত্যন্ত উচ্চ-ঝুঁকিতে, ৩৪টি দেশ উচ্চ-ঝুঁকিতে এবং ৮টি দেশ মাঝারি/কম ঝুঁকিতে রয়েছে। সকল স্বল্পোন্নত দেশে জলবায়ু অর্থায়নের ৭০%-এর বেশি ঋণ হিসেবে আসে, যা প্যারিস চুক্তির ‘দূষণকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়’ নীতি এবং জলবায়ু ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের ২০২৫ সালের রায়ের সরাসরি লঙ্ঘন। কপ-৩০ সম্মেলনে এই সূচকে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক চিত্রসহ পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক সংস্করণ প্রকাশ করা হবে।
বিশ্লেষকরা যা বলছেন:
বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থা ঋণ-নির্ভর, ধীরগতির এবং জীবন রক্ষাকারী অভিযোজন কার্যক্রমের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। সরকারি অর্থায়ন দেরিতে এবং ঋণ হিসেবে আসায় সাধারণ মানুষ নিজ খরচে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে জলবায়ু অর্থায়ন দেখানোয় ঋণের বোঝা বাড়ছে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা না নিলে দেশের আর্থিক সক্ষমতা সংকুচিত হবে, সামাজিক খাতে ব্যয় হ্রাস পাবে এবং জলবায়ু ঘটিত দুর্যোগের প্রভাব আরও মারাত্মক হবে। ক্রমবর্ধমান ঋণের ফাঁদ এড়াতে অনুদান-ভিত্তিক অর্থায়ন এবং স্বচ্ছ শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য। ন্যায্য জলবায়ু অর্থায়নের পথ (প্রাকৃতিক অধিকার ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা) বাংলাদেশ ‘প্রাকৃতিক অধিকার ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে একটি বাস্তবসম্মত পথ দেখাচ্ছে। এই শাসনব্যবস্থা মানুষ এবং প্রকৃতির অস্তিত্ব রক্ষা, পুনরুদ্ধার ও বিকাশের সহজাত অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং জলবায়ু অর্থায়নকে দান হিসেবে না দেখে একটি বাধ্যবাধকতা হিসেবে বিবেচনা করে। এই ব্যবস্থার অধীনে, অভিযোজন এবং ক্ষয়ক্ষতি (লস অ্যান্ড ড্যামেজ) বিষয়ক সহায়তা অবশ্যই ঋণমুক্ত হতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে এর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং ভুল বরাদ্দ রোধে স্বচ্ছ নিয়ম থাকতে হবে।
এ বিষয়ে চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ প্রধান নির্বাহী এর এম. জাকির হোসেন খান বলেন, “দৃঢ় অঙ্গীকার ও স্পষ্ট শাসনব্যবস্থা না থাকলে কপ-২৯ এ ঘোষিত ১ বিলিয়ন ডলারের ‘ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যাকশন ফান্ড’ উচ্চাশাই থেকে যাবে; ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য প্রকৃত লাইফলাইনে পরিণত হবে না।”
বাংলাদেশের করণীয়:
অভিযোজন খাতের কমপক্ষে ৭০% এবং ক্ষয়ক্ষতি খাতের ১০০% অর্থায়ন অনুদান হিসেবে আসতে হবে। শুধুমাত্র যেখানে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ও ন্যায্য, সেখানেই সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণযোগ্য। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঋণ বাতিল করতে হবে এবং প্রকৃতি/জলবায়ু সুরক্ষার বিনিময়ে ঋণ মওকুফ (debt-for-nature/climate swaps) কার্যক্রম বাড়াতে হবে। সরাসরি স্থানীয় পর্যায়ে অর্থায়ন: পৌরসভা, স্থানীয় সরকার এবং কমিউনিটিকে সহজসরল প্রক্রিয়ায় সরাসরি অর্থায়ন করতে হবে এবং উপ-জাতীয় পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। অনুদান বৃদ্ধি, অভিযোজন খাতে ভারসাম্য আনা, জীবাশ্ম জ্বালানিতে ভুল বরাদ্দ বন্ধ এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনে দেশীয় প্ল্যাটফর্মকে সমর্থন করতে হবে। কার্বন প্রাইসিং এবং লেনদেন শুল্কের মাধ্যমে একটি বৈশ্বিক অনুদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা শর্তহীনভাবে দেশীয় মালিকানায় জলবায়ু সহনশীলতা প্রকল্পে অর্থায়ন করবে। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডকে ‘বাংলাদেশ ন্যাচারাল রাইটস ফান্ড (বিএনআরএফ)’-এ রূপান্তরিত করতে হবে, যা অধিকার-ভিত্তিক বরাদ্দ এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। দূষণ কর ও কার্বন প্রাইসিংয়ের মতো নতুন অভ্যন্তরীণ উৎসও এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ড. সাইমন পারভেজ বলেন, “বাংলাদেশের নিঃসরণ কম, প্রভাব বেশি। জলবায়ু অর্থায়ন ঋণ–নির্ভরতা থেকে সরে ন্যায় ও সমতার দিকে যেতে হবে—স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বাস্তব অভিযোজন সহায়তা সহ। প্রকৃতি–ভিত্তিক সমাধান, নৌপথ পুনরুদ্ধার, নবায়নযোগ্য শক্তি, জলবায়ু–স্মার্ট কৃষি—এসব কাজে বিশেষজ্ঞতা, জাতীয় অঙ্গীকার ও বৈশ্বিক সংহতি প্রয়োজন। জলবায়ু ঋণের যুগ শেষ হোক, জলবায়ু ন্যায়ের যুগ শুরু হোক।”