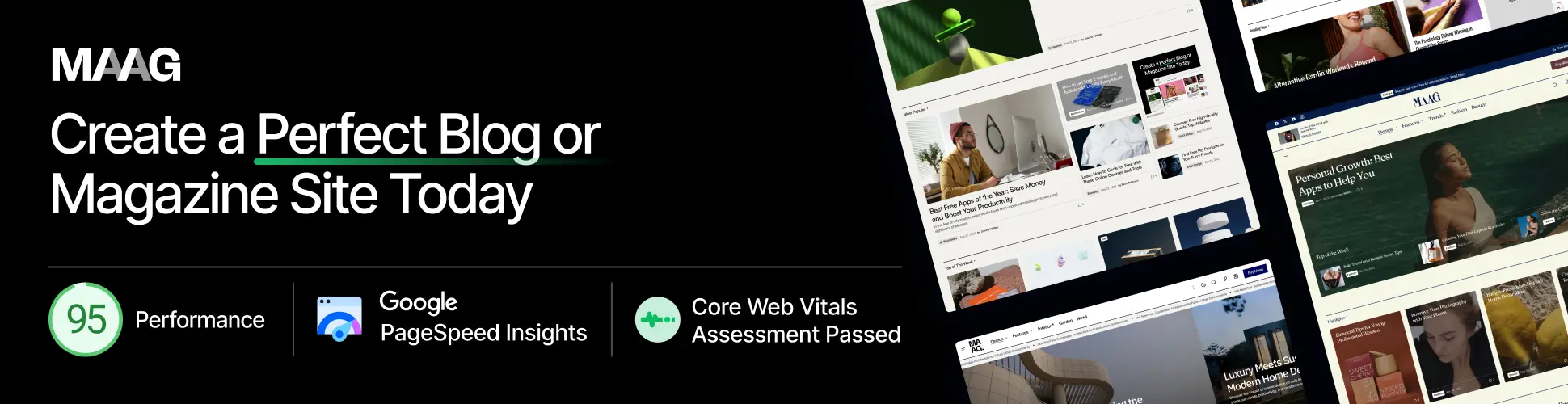রোডম্যাপ ঘিরেই আমূল সংস্কার বিচার বিভাগে। যার পূর্ণতা পাবে বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর প্রধান বিচারপতির পদে আসীন হন বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি বিচার বিভাগ সংস্কারে ঘোষণা করেন রোডম্যাপ। বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয়, বিচারক নিয়োগে আইন, পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠাসহ সংস্কারের রূপরেখা তুলে ধরেন বিচার বিভাগের এই অভিভাবক। প্রধান বিচারপতির সংস্কারের রূপরেখা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা পালন করছে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নের্তৃত্বাধীন অন্তবর্তি সরকার। প্রধান বিচারপতির নেওয়া পদক্ষেপগুলোকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহন করে তা বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সহায়তা করছে সরকারের আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, যেসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হয়েছে তার সুফল পাবে বিচারপ্রার্থী জনগণ। এজন্য বিচারক সংকট ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা নিরসন করে পূর্ণ উদ্যামে কাজ শুরু হলেই দ্রুত বিচার পাবে বিচারপ্রার্থী জনগণ। ফলে বিচারপ্রার্থীকে বছরের পর বছর আদালতের বারান্দায় ঘুরতে হবে না। তবে এসব সংস্কার কতটা টেকসই হবে তা নির্ভর করছে আগামী রাজনৈতিক সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তের উপর।
তবে এসব সংস্কারের পাশাপাশি ন্যায় বিচারের সমান সুযোগ সৃষ্টি, বিচারপ্রার্থীর নিরাপত্তা, বিচার প্রক্রিয়ায় যে জটিলতা তা নিরসনের দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারন প্রতি বছরই বাড়ছে মামলা জট। কোনভাবেই এই সংখ্যা কমানো যাচ্ছে না। বর্তমানে দেশের আদালতসূমহে ৪৪ লাখ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এত মামলা কিভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে তা ভাবিয়ে তুলছে বিচার প্রশাসনকেও।
আইনজ্ঞরা বলছেন, যত সংস্কারই হোক না কেন দ্রূত বিচার পাইয়ে দিতে বিচারকদেরকেই স্বাধীন ও পক্ষপাতহীনভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হবে। অতীতে দেখতে পেয়েছি বিচারকরা সময়মত এজলাসে বসেন না। দিনের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় অনেকটাই। ফলে মামলা নিষ্পত্তিতে ভাটা পড়ে। বাড়ে জট। কিভাবে এই মামলা জট কমিয়ে বিচারপ্রার্থীকে দ্রæত বিচার পাইয়ে দেওয়া সম্ভব হবে সেদিকে নজর দিতে হবে বিচারকদেরকেই।
আইনজ্ঞরা মনে করেন, অতীতে বিচার ব্যবস্থা নিয়ে জনমনে যে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করাটাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। আইন করে পূর্ণস্বাধীনতা দেওয়া হলেও যদি বিচারকরা চিন্তা-চেতনা ও মননে স্বাধীন না হন তাহলে কোন সংস্কারই কাজে আসবে না। সেজন্য বিচারকদেরকে ক্ষমতার রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা করে ন্যায় বিচার নিশ্চিতে সর্বদাই কাজ করে যেতে হবে। তাহলে ঘুরে দাড়াবে বিচার বিভাগ।
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও সংস্কার নিয়ে আইন বিশ্লেষক ও গবেষক সাবেক জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ ফউজুল আজিম ইত্তেফাককে বলেন, সংস্কারের কিছু ভালো ও মন্দ দিক রয়েছে। এসব সংস্কার করার আগে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে করা উচিত ছিলো। যাতে বিচারপ্রার্থী জনগণ তাৎক্ষণিক সুফল পান। কিছু সংস্কার হয়েছেন যার সুফল এখনই পাবে না জনগণ। তবে তিনি মনে করেন, বিচারের মৌলিক সংস্কার করা দরকার। যেমন জামিনের জন্য গ্রাম থেকে একজন ব্যক্তিকে এখনো আপিল বিভাগ পর্যন্ত আসতে হচ্ছে। অথচ জামিনের বিষয়টি জেলা আদালত পর্যায়েই নিষ্পত্তি করার পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার ছিলো। তাহলে প্রকৃতপক্ষে বিচারপ্রার্থী জনগণ উপকৃত হত।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহফুজুর রহমান মিলন ইত্তেফাককে বলেন, যত সংস্কারই করা হোক না কেন জনগনের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে সেগুলো বাস্তবায়নে আন্তরিকতা দেখাতে হবে। যদি রাজনৈতিক সরকার সে পথে না হাটেন তাহলে এসব সংস্কার বিফলে যাবে। তিনি বলেন, আমি প্রত্যাশা করি আগামীতে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের উচিত এসব সংস্কার কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া। তাহলে বিচারপ্রার্থীরা উপকৃত হবেন।
হাইকোর্টের স্পেশাল অফিসার মো: মোয়াজ্জেম হোছাইন ইত্তেফাককে বলেন, মাননীয় প্রধান বিচারপতি ঘোষিত রোডম্যাপের আলোকে বিচার বিভাগে বড় ধরনের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজ ও চলমান আচ্ছে। যেসব সংস্কার হয়েছে তার সুফল পাচ্ছে বিচারপ্রার্থীরা। বাকি সংস্কারগুলো সম্পন্ন হলে বদলে যাবে বিচার বিভাগ। জনগনের আস্থা ফিরবে এই বিভাগের উপর।
ঢাকার আদালতে বিচার বিভাগের সংস্কার নিয়ে কথা হয় বদরুল নামে এক বিচারপ্রার্থীর সঙ্গে। এসেছেন ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থেকে। তিনি ইত্তেফাককে বলেন, আমি এত সংস্কার বুঝি না। আমার দরকার কত কম সময়ে আমি বিচার পাব। কত দ্রæত নিষ্পত্তি হবে মামলাটা। নইলে বছরের পর বছর কোর্টের বারান্দায় ঘুরতে হবে আমাকে। আর অর্থ ব্যয় তো রয়েছেই।
প্রসঙ্গত: শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা বাতিল করে আওয়ামী লীগ সরকার। ২০২৪ সালে এক রিট মামলার রায়ে কোটা পদ্ধতি ফিরিয়ে আনে হাইকোর্ট। এ নিয়ে আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীরা। সেই আন্দোলন এক পর্যায়ে রূপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। দীর্ঘ ৩৬ দিনের আন্দোলনে প্রাণ হারায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও জনতা। ছাত্র-জনতার রক্তক্ষীয় সেই সংগ্রামের মুখে পতন হয় আওয়ামী লীগ সরকারের। তিনদিন পর গত বছরের ৮ আগস্ট যাত্রা শুরু করে অন্তবর্তি সরকার। দায়িত্ব গ্রহন করেই অন্তবর্তি সরকার বিচার বিভাগসহ নানা সেক্টরে সংস্কারের লক্ষ্যে গঠন করে একাধিক সংস্কার কমিশন। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দেওয়ার আগেই প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ গত বছরের ২১ সেপ্টেম্বর বিচার বিভাগ সংস্কারে রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। রোডম্যাপেও সংস্কারের নানা প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়।
অপরদিকে গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে বিচারহীনতার সংস্কৃতি, বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা, মামলা জট হ্রাস, আদালতের বিকেন্দ্রীকরন, মোবাইল কোর্ট, গ্রাম আদালত, আইন পেশা ও শিক্ষার সংস্কারসহ ৩১টি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সহকারে নানা সুপারিশ তুলে ধরে সরকারের কাছে।
কেন এই সংস্কার:
অতীতে দেখা গেছে রাজনৈতিক সরকারগুলো ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখায় সচেষ্ট ছিলো। নানা উপায়ে সেই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলত। কখনো সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে পছন্দের বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি করে অঘোষিত সেই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলেছে। হাইকোর্ট বিভাগে প্রায়শই জ্যেষ্ঠ বিচারপতিদেরকে রিট ও ফৌজদারি মোশন শুনানি এখতিয়ার না দিয়ে এই চেষ্টা হয়েছে। অথবা গুরুত্বপূর্ণ মামলায় কনিষ্ঠ বিচারপতিরা বিব্রতবোধ করে সেই চেষ্টাকে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। আবার বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয়েছিলো জাতীয় সংসদের কাছে।
যদিও সুপ্রিম কোর্টের দৃঢ় ভূমিকার কারনে ২০১৭ সালে বিচারপতি অপসারন সংক্রান্ত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অসাংবিধানিক ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষনা করে আপিল বিভাগ। ফিরিয়ে আনা হয় সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের বিধান। যে বিধানের মধ্য দিয়ে পুনরায় কার্যকর হয় প্রধান বিচারপতির নের্তৃত্বে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। যে কাউন্সিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের দুর্নীতি ও অসদাচরণের অনুসন্ধান ও তদন্ত করে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট দিয়ে থাকেন। যদি দুর্নীতি বা অসদাচরণের প্রমাণ মেলে তখন সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারন করেন রাষ্ট্রপতি।
এছাড়া অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদায়ন ও পদোন্নতিতে ‘পিক এন্ড চুজ’ নীতি গ্রহন করেছিলো বিগত সরকারগুলো। সরকারের আজ্ঞাবহ বিচারকরা অধস্তন আদালতের গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক পদগুলোতে পদায়িত হয়েছিলেন। যারা আইন মেনে রায় বা আদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাদেরকে দূর-দূরান্তে বদলি করে হেনস্থার ঘটনাও ঘটেছে। এভাবেই চলছিলো বিচার বিভাগ।
কিন্তু ছাত্র-জনতার একটি গণঅভ্যুত্থান পাল্টে দিয়েছে সকল হিসাব-নিকাশ। আন্দোলনের মুখে গত বছরের ১০ আগস্ট পদত্যাগে বাধ্য হন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ আপিল বিভাগের আরো পাঁচ বিচারপতি। পদত্যাগেরই দিনই প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয় হাইকোর্টের জ্যেষ্ঠ বিচারক বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদকে। শপথের পর আইনজীবীদের সংবর্ধনার জবাবে তখন প্রধান বিচারপতি রেফাত আহমেদ বলেন,“এই মুহূর্তে আমরা এক ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছি। বিগত বছরগুলোতে বিচার প্রক্রিয়ায়, আমাদের বিচারবোধ, ন্যায়বিচারের মূল্যবোধকে বিনষ্ট ও বিকৃত করা হয়েছে। সততার বদলে শঠতা, অধিকারের বদলে বঞ্চনা, বিচারের বদলে নিপীড়ন, আশ্রয়ের বদলে নির্যাতনকে স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত করা হয়েছে। অথচ এরকম সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা চাইনি। এই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েই আমাদেরকে নতুন যাত্রা শুরু করতে হবে।’
দায়িত্ব গ্রহনের এক মাসের মাথায় গত বছরের ২১ সেপ্টেম্বর রোডম্যাপ ঘোষণা করেন তিনি। সেখানে তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রীকরণ ও বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক পৃথকীকরণ এর বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করেন। রোডম্যাপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিচার বিভাগের অর্থপূর্ণ সংস্কার নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার রূপরেখা ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল রোডম্যাপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখারও আশ্বাস দেন। পরবর্তীকালে আইন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে ধরনের সমর্থন প্রয়োজন রোডম্যাপ বাস্তবায়নে সব ধরনের সহযোগিতা করেছে ও করছে মন্ত্রণালয়। ফলে সংস্কার কাজ এগিয়েছে দ্রুত। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার দোহাই দিয়ে কোন কাজই আটকে থাকেনি এ সময়ে। ফলে রাজনৈতিক সরকারগুলোর সময়ে যে অগ্রগতি শুধু কাগজে কলমে বা বক্তব্যে সীমাবদ্ধ ছিলো তা এখন অনেকটাই বাস্তবে রূপ পেয়েছে ও পাচ্ছে। শুধু সরকারই নয়, বিচার বিভাগ সংস্কারে প্রধান বিচারপতি যে নের্তৃত্ব দিয়েছেন তাতে ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) সহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো সহায়ক ভ‚মিকা পালন করছেন।
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের আর্থিক স্বাধীনতা কার হাতে:
রোডম্যাপে উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে ছিলো বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অধীনে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা। এই সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের প্রথম কোন প্রধান বিচারপতি গত বছরের ২৭ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট হতে পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠান। প্রস্তাবে সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ যথাযথরূপে পালনের উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশের খসড়া, প্রস্তাবিত সচিবালয়ের অর্গানোগ্রাম এবং রুল অব বিজনেস ও অ্যালোকেশন অব বিজনেসের সম্ভাব্য সংস্কার সম্পর্কে পরিপূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের অন্তর্গত ‘অন্তবর্তীকালীন ও সাময়িক বিধানাবলীর দফা ৬(৬)অনুযায়ী অধস্তন আদালত সম্পর্কিত সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের বিধানাবলী যথা শীঘ্রসম্ভব বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্তরূপ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার আলোকে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হলে অধস্তন আদালতের বিচারকগণের পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা, ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটবে এবং বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাঠানোর পরই এ সংক্রান্ত খসড়া সুপ্রিম কোর্ট থেকে আইন মন্ত্রনালয়ে পাঠানো হয়। সেই খসড়া কিছুটা সংশোধন করে চূড়ান্ত করে আইন মন্ত্রণালয়। যেখানে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় নামে বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির হাতে রাখা হয়।
এদিকে বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় বাধা ছিলো বিদ্যমান সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ। যে অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজটি রাষ্ট্রপতির নামে আইন মন্ত্রণালয় করে থাকত সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে। ফলে বিচার বিভাগে এক ধরনের দ্বৈতশাসন বিরাজমান ছিলো। এই দ্বৈতশাসন নিয়ে অতীতে অনেক প্রধান বিচারপতি বক্তব্যও রেখেছেন। কিন্তু দ্বৈতশাসন অবসানে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ সুপ্রিম কোর্টের সকল বিচারকদের মতামত নিয়ে অন্তবর্তি সরকারকে সরাসরি লিখিত প্রস্তাব পাঠান সরকারকে। সুপ্রিম কোর্টের লিখিত প্রস্তাব পেয়ে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেয় আইন মন্ত্রণালয়।
গত ২ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রিট মামলায় দেওয়া রায়ে তিন মাসের মধ্যে বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় স্থাপনে সরকারকে নির্দেশ প্রদান করেন। একইসঙ্গে বিদ্যমান সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদকে সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করে বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যাস্ত করেন। যার মধ্য দিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয় ৭২’র সালের আদি সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ। যে অনুচ্ছেদে বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যাস্ত ছিলো। পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সাংবিধানিক বাধা ছিলো হাইকোর্টের রায়ের ফলে তাও দূর হয়ে যায়। কিন্তু এরপরেও রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাচে সচিবালয় প্রতিষ্ঠায় নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অদৃশ্য চেষ্টা চলে। তবে সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রনীত খসড়া অধ্যাদেশে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। এখন সচিবালয়ের আর্থিক স্বাধীনতা কার হাতে থাকবে সেই বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের মত নিয়ে তা পুনরায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদে যাবে। সেখানে অনুমোদনের পরই অধ্যাদেশ জারি করবেন রাষ্ট্রপতি। এরপরই তা গেজেট আকারে প্রকাশ করবে আইন মন্ত্রণালয়। গেজেট প্রকাশের পরই জানা যাবে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের অধ্যাদেশে আর্থিক স্বাধীনতা কার হাতে ন্যাস্ত থাকছে।
এ প্রসঙ্গে সাবেক জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ ড. মো. শাহজাহান সাজু ইত্তেফাককে বলেন, ১৯৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর মাসদার হোসেন মামলার রায়ে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরনের কথা বলা হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুটি রাজনৈতিক সরকার দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকলেও সর্বোচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়নের দিকে তারা মনোযোগী হয়নি। ওই রায় দেওয়ার আট বছর পর ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আমলাততন্ত্রের বাধা উপেক্ষা করে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয় বিচার বিভাগকে। কিন্তু গত ১৮ বছরেও প্রতিষ্ঠা করা যায়নি বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয়। এই সচিবালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে টানাপোড়ন চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। তিনি বলেন, সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বিচারিক কাজের পাশাপাশি আর্থিত স্বাধীনতাও নিশ্চিত করতে হবে। বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয়ের আর্থিক স্বাধীনতা না থাকলে ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী থাকতে হবে। আর সরকারের মুখাপেক্ষী হলেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় সরকারের যে অদৃশ্য হস্তক্ষেপ তার প্রভাব পড়বে। সেজন্য পৃথক সচিবালয়ের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। যদি এটা করা সম্ভব না হয় তাহলে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা ও পৃথককরণ কোনটাই অর্থবহ হবে না।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বলছেন, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের আর্থিক স্বাধীনতা সরকার নিজের হাতে রেখে দিলে তা মাসদার হোসেন মামলার রায়ের পরিপন্থী হবে। এজন্য সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়কে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করাটা জরুরি।
সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ:
রাজনৈতিক প্রভাব বলয় মুক্ত থেকে সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগে আইন প্রণয়ন ছিলো দীর্ঘদিনের দাবি। সেই লক্ষ্যপূরণে রোডম্যাপে বিচারক নিয়োগে আইন প্রণয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। এ লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে যে সকল প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় তা গভীরভাবে বিশ্লেষণপূর্বক এ সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশের খসড়া প্রস্তুত করে গত বছরের ২৮ অক্টোবর আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন থেকেও এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশের একটি খসড়া সরকারের কাছে পাঠানো হয়। দুটি খসড়া যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে উপদেষ্টা পরিষদে ‘সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ’ এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়। ২১ জানুয়ারি অধ্যাদেশটি পাশ হয়। ইতোমধ্যে এই অধ্যাদেশের আওতায় গত ২৫ আগস্ট হাইকোর্টে ২৫ জন অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা বলছেন, অতীতের যে কোন নিয়োগের চাইতে এবারের বিচারক নিয়োগ অনেকটাই ভালো হয়েছে। অতীতে অনেক অযোগ্য ও অদক্ষদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যার ভুক্তভোগী হয়েছে দেশের বিচারপ্রার্থী জনগণ।
প্রসঙ্গত: ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এরকম একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ করা হয় উচ্চ আদালতে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে অধ্যাদেশটি সংসদে পাস না করায় তা আইনে পরিণত হয় নাই। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায় অধ্যাদেশটি। পরে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যোগ্যতা, সততা ও দক্ষতা বিবেচনা না করেই অনেককেই বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়। যার প্রতিবাদ করেছিলো সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি।
এ প্রসঙ্গে সাবেক জেলা জজ ফাওজুল আজিম বলেন, সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগের যে অধ্যাদেশ করা হয়েছে সেখানে উচ্চ আদালতে বিচারক হতে একজন জেলা জজকে দরখাস্ত করতে হয়। একজন জেলা জজের দীর্ঘ বিচারিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাকে কেন দরখাস্ত করে উচ্চ আদালতের বিচারক হতে। অধ্যাদেশে এ বিষয়টি পুনবির্বেচনা হওয়া উচিত।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারক অপসারন ক্ষমতা কাউন্সিলের হাতে:
বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানে ষোড়শ সংশোধনী এনে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক অপসারন ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে অর্পণ করে। কিন্তু এক রিট মামলায় ২০১৬ সালে হাইকোর্ট এই সংশোধনীকে অবৈধ ও সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করে বিচারপতি অপসারন ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের হাতে ন্যাস্ত করে। ওই রায় বহাল রাখে আপিল বিভাগ। রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দাখিল করে তৎকালীন সরকার। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নের্তৃত্বাধীন সাত বিচারপতির আপিল বেঞ্চ গত বছরের ২০ অক্টোবর ষোড়শ সংশোধনী ফিরিয়ে আনা সংক্রান্ত সরকারের রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেন। ফলে সংবিধানে পুনরুজ্জীবিত হয় সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের বিধান।
রিভিউর রায়ের পর্যবেক্ষণে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী বলেছেন, ‘‘ষোড়শ সংশোধনীর মামলার সারমর্ম কী ছিল? আমার মতে, এটি ছিল একটি স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী সরকারের প্রচেষ্টা, সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল থেকে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সংসদের হাতে ন্যস্ত করার, যার ফলে বিচারকদের স্বাধীনতা ঝুঁকির মুখে পড়ে। অন্য কথায়, যদি কোনও বিচারক তার দায়িত্ব পালনের সময় সরকারের ক্রোধ বা বিরোধিতার শিকার হন, তাহলে সংসদ সদস্যরা তাকে কলমের আঘাতে পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন। গণতান্ত্রিক সমাজে কি এমন পরিস্থিতি অনুমোদিত বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আমার বিবেচনায়, যেমনটি আমার বিদ্বান ভাইয়েরা (বিচারপতি) তাদের নিজ নিজ রায়ে বলেছেন, এর উত্তরটি হলো জোরালোভাবে ‘না’।’
রায়ের পর্যবেক্ষণে এই বিচারপতি বলেন, ‘‘বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হলো আইনের শাসনের ‘অপরিহার্য শর্ত’, যা যেকোনও গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি গঠন করে। আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে অর্পণ করার প্রক্রিয়া বিচার বিভাগের ওপর সাধারণ জনগণের আস্থা নষ্ট করে। অতএব, বিচারকদের দায়িত্ব পালনের সময়, ন্যায়বিচারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের জন্য তাদের মেয়াদ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।’’
এই রায়ের পর কার্যকর করা হয় সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। যে কাউন্সিলের তদন্তের মুখে পড়েন হাইকোর্টের ১২ বিচারপতি। ইতিমধ্যে কাউন্সিল আটজন বিচারপতির অসদাচরণের তদন্ত করে কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করেছে। ওই সুপারিশের পর দু’জন বিচারপতিকে অপসারন করেছেন রাষ্ট্রপতি। দু’জন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। আবার তদন্ত চলা অবস্থায় দু’জন বিচারপতি অবসরে যান। আর দু’জন বিচারপতিকে স্থায়ী না করায় তারাও তদন্ত চলা অবস্থায় অবসরে যান।
আইনজ্ঞরা বলছেন, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিচারিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেউ অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে পার পেয়ে যাবেন এমনটা মনে করার সুযোগ নাই। কারন বিচারিক স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয় এটা মনে রাখা উচিত।
দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত পৃথককরন:
অতীতে অধস্তন আদালতের বিচারকগণ একই সঙ্গে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় ধরনের মামলার বিচার কাজ পরিচালনা করতেন। এতে মামলা নিষ্পত্তিতে ভাটা পড়ত। বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি বাড়ত। এই ভোগান্তি নিরসনে পদক্ষেপ নিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে মামলা জট নিরসন ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে সারা দেশে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত পৃথকের গেজেট জারি করা হয়েছে। এছাড়া মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে পৃথক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু আদালত শুধুমাত্র বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং কিছু আদালত শুধুমাত্র আমলি আদালত হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এদিকে শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালসহ বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৮৭১টি নতুন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
আদালত পৃথককরন সম্পর্কে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মাসুদ ইত্তেফাককে বলেন, সরকার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উভয় প্রকৃতির মামলার নিষ্পত্তির হার বাড়বে। ভোগান্তি কমবে জনগণের।
তবে এই পদ্ধতি কার্যকরে অধিক সংখ্যক বিচারক নিয়োগ দিতে হবে বলে মনে করেন সাবেক জেলা ও দায়রা জজ মো. শাহজাহান সাজু। তিনি বলেন, যত বেশি আদালত কার্যকর থাকবে তত বেশি মামলা নিষ্পত্তি হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ ও অবকাঠামোগত যে অঅপ্রতুলতা রয়েছে তা নিরসন হলেই আদালত পৃথকের সুফল পাবে জনগণ।
সাক্ষী না আসা মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে সিআরপিসির দুটি ধারা প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা জরুরি:
অধস্তন আদালতগুলোতে লাখ লাখ মামলা বিচারাধীন। বিচারাধীন এসব মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে বছরের পর বছর ধরে। বিপুল সংখ্যক অনিষ্পন্ন মামলার জট থেকে বিচার বিভাগ ও বিচারপ্রার্থী জনগণকে কিভাবে মুক্ত করতে নানা সুপারিশ করেছে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। কমিশনের প্রস্তাব, যেসব মামলার বিচার শুরু হয়েছে অর্থচ দীর্ঘদিন সাক্ষী আসছে না সেসব মামলার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৪৯ ও ২৬৫(এইচ) ধারা প্রয়োগ করতে হবে। যার মাধ্যমে সাক্ষ্য কার্যক্রম বন্ধ করে চ‚ড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আদালতকে যাতে সরকারি আইন কর্মকর্তা অনুরোধ করেন এমন নির্দেশনা জারি করতে হবে। এতে মামলা জট কিছুটা হলেও হ্রাস করা সম্ভব হবে।
আইনজ্ঞরা বলছেন, এই ধারা প্রয়োগের আগে যাদের উপর সাক্ষী হাজিরার দায়িত্ব রয়েছে তারা দায়িত্বে অবহেলা করলে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। নইলে ন্যায় বিচার পরাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে গত বছর ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল থেকে ৪৬টি খুনের মামলায় কোন আসামি সাজা পাননি। ২০ বছরের এসব পুরনো মামলায় সাক্ষী দিতে হাজির হননি বাদী, লাশের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক, তদন্ত কর্মকর্তাসহ গুরুত্বফ‚ণৃ সাক্ষীরা। ফলে চার মাসে এসব মামলা থেকে খালাস পেয়ে যান চার্জশিটভুক্ত ২০০ আসামি।
বিচারক সংকট ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা জরুরি:
দেশে বিচারক সংকট তীব্র। প্রায় ১৮ কোটি জনগণের বিপরীতে বিচারকের সংখ্যা মাত্র ২ হাজার ৩০৭ জন। বিচারক প্রতি মামলা প্রায় দুই হাজারের মত। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৬ হাজার ৬৬৭ জনে ১ জন বিচারক এবং যুক্তরাজ্যে প্রতি ১৩ হাজার ১৪০ জনে ১ জন বিচারক রয়েছেন। আর বাংলাদেশে এক লাখ মানুষের জন্য বিচারক রয়েছেন একজন। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলেছেন। তারা সরকারকে বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬ হাজারে উন্নীত করতে বলেছেন। তাতে সংকট কিছুটা কমবে বলে ধারনা। এছাড়া কমিশন দেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় যে ২৩ জেলায় এখনো ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়নি সেগুলোর নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে বলেছে। ৩৪টি উপজেলায় অবস্থিত ৫১টি চৌকি আদালতের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণের নিমিত্তে একটি প্রকল্প নিতে সুপারিশ করেছে। জেলা জজ আদালতের আওতাধীন ৬৬টি এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আওতাধীন ৬৪টি আদালতের জন্য জরুরি ভিত্তিতে এজলাস নির্মাণ করা জরুরি বলে মনে করছেন বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। এসব অবকাঠামো নির্মাণ হলেই বন্ধ হবে ভাগাভাগি করে এজলাস ব্যবহারের প্রবণতা। বাড়বে মামলার নিষ্পত্তির হার। আর বিচারকদের আবাসনের জন্য জেলা পর্যায়ে পৃথক জুডিসিয়াল কমপ্লেক্স স্থ্পান করার সুপারিশ করেছে কমিশন।
বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য ৩টি বিধিমালা প্রণয়ন:
অতীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল বলে নিম্ন আদালতের বিচারকের পদ সৃজনে বিলম্ব হতো। বৃদ্ধি পেত মামলাজট। এখন সুপ্রিম কোর্টের অধীনে বিশেষ কমিটিকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে বিচারিক পদ সৃজন সহজ হয়েছে। নতুন বিধি জারির দুই সপ্তাহের মধ্যে ২৩২ বিচারকের পদ সৃজিত হয়েছে। এছাড়া বিচারকদের স্বাধীনতা নিশ্চিতে বিচারকদের বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি ও চাকরির অন্যান্য শর্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। আগে স্থানীয়ভাবে আদালতের সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ হওয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও দুর্নীতি হতো। বর্তমানে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগের বিধান করা হয়েছে। ফলে সহায়ক কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠত তা থেকে বিচার বিভাগ মুক্ত থাকতে পারবে বলে মনে করেন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা।
শাখার অনিয়ম রোধে কঠোর হওয়া প্রয়োজন:
বিচারপ্রার্থী জনগণকে সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির কোনো শাখায় সেবা গ্রহণে কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে বা সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হলে উক্ত সেবাগ্রহীতাকে সহায়তা করার নিমিত্ত একটি হেল্পলাইন নাম্বার চালু করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতির উদ্যোগে এ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়। সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতি রবিবার হতে বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা হতে বেলা ৪ টা পর্যন্ত উক্ত হেল্পলাইন সার্ভিস হতে সেবা গ্রহণ করেন বিচারপ্রার্থীরা। একইসাথে হেল্পলাইন নাম্বারে হোয়াটসঅয়াপ ও মোবাইলঅ্যাপ সার্ভিস চালু রয়েছে। তবে এসব সংস্কারের পাশাপাশি দেশের আদালতের বিভিন্ন শাখাগুলোতে যেসব অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় তা রোধে বিচার প্রশাসনকে আরো কঠোর হওয়া দরকার বলে মনে করেন সাধারণ আইনজীবীরা।